Sudeep Chatterjee's Blog, page 16
August 1, 2020
'মগ- মোগল- পর্তুগিজ- ব্রিটিশ- ওলন্দাজ- বাঙালি' : এক ঐতিহাসিক ভুরাজনৈতিক উপন্যাস

আন্দালুসিয়ার শহরে একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে কয়েকটা বই নজরে পড়েছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজদের ভারতবর্ষে আসা নিয়ে লেখা, বিশেষত বাংলা ও বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের নানা দেশ আর রাজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করার কাহিনী। মুর রাজাদের জাহাজ ব্যবহার করে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীরা ভারতে পাড়ি দিয়েছিল, এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী সময়ে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল জলদস্যু হিসেবে। স্বাভাবিকভাবেই বইগুলো ছিল স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষায় লেখা।
যাই হোক, বাংলার এই ইতিহাস নিয়ে স্পেনের দোকানে সারি সারি বই দেখে আমি বেশ অবাকই হয়েছিলাম। সেই যুগের ইতিহাস ও পর্তুগিজ শাসকদের বাংলা ঔপনিবেশবাদ গড়ে তোলা নিয়ে বাংলায় খুব কম লেখাই চোখে পড়েছে। সমসাময়িক কালে এই প্রথম একটা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এসে সেই জায়গাটা ভরাট করল।
‘পাইয়া ফিরিঙ্গ ডর’ এক নিশ্বাসে পড়ে ওঠার জন্যে লেখা হয়নি। মগ, পর্তুগিজ, আরাকান, মোগলরা যখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সেই সময়টাকে পুঙ্খানুুঙ্খভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন রাজর্ষি। বিভিন্ন চরিত্র ও বহুস্তরীয় দৃষ্টিকোণ ফুটে উঠেছে কাহিনীর আঁকেবাঁকে। নন লিনিয়ার ন্যারেটিভকে দক্ষ ভাবে ব্যবহার করেছেন লেখক, ফলে বিভিন্ন কাহিনীর মাঝে বুনে তোলা সূত্র জুড়ে গেছে একে অপরের সঙ্গে, সময়ের ফাটলগুলো ভরাট হয়ে গেছে সাবলীলভাবে।
লেখাটা পড়তে আমার বেশ সময় লেগেছে, তার প্রধান কারণ এর ব্যাপ্তি ও ডিটেইটিং। এই আখ্যানের ভাঁজে ভাঁজে সূক্ষ্ম কারুকাজ আছে, নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রতিটা পরিসর, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের সামাজিক জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি। বস্তুত এই বিন্দুগুলো এই লেখার স্ট্রং পয়েন্ট, আগ্রহ থাকলে এই জায়গাগুলো দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মন দিয়ে পড়লে বোঝা যায়, তথ্যের খুঁটিনাটি ও সত্যতা সম্পর্কে লেখক কতটা যত্নবান! রাজর্ষি কোথাও ভাষাকে অযথা জটিল করেননি, কিন্তু বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা আর পরিবেশ তৈরি করার ক্ষমতা নিয়ে কোন কথা হবে না।
'পাইয়া ফিরিঙ্গ ডর' কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেতেই পারে, আবার সামাজিক অথবা প্রেমের উপন্যাস বললেও ভুল হবে না। এই বহুকৌণিক কাহিনীতে যেমন টিবাও, ভিশকু আর কাবালহোর মতন পর্তুগিজ দস্যু আছে, সেরকমই আছে নগেনের মত ভাগ্যান্বেষী বাঙালি, ধনী পরিবারের ছেলে শ্যামল, আধা ফিরিঙ্গি ওফেলিয়া। এমনকি জলার পেত্নী কর্পূর্মঞ্জরীও আছে। (এরকম বাস্তবভিত্তিক লিটারারি উপন্যাসে পেত্নী দেখে সত্যিই ভড়কে গিয়েছিলাম, ব্যাপারটা মেটাফর কি না বোঝার চেষ্টা করছি, ইতিমধ্যে আবিষ্কার করলাম এই অলৌকিক আখ্যান সহজ ভাবে জুড়ে গেছে মূল কাহিনীর সঙ্গে, কোথাও খাপছাড়া মনে হয়নি। সুতরাং সেই চিন্তায় অব্যাহতি দিলাম )
যাই হোক, আমার মতে, পাইয়া ফিরিঙ্গ ডর আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক উপন্যাস। আরো ভাল করে বলতে গেলে ভূরাজনৈতিক উপন্যাস। সপ্তদশ শতাব্দীতে জিও পলিটিকাল ফিকশন লেখা হত না নিশ্চয়ই, সে অর্থে এই কাহিনী বিরল। ক্ষমতা লাভ ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পাশাপাশি রাজনৈতিক সম্পর্ক, যুদ্ধের পরিকল্পনা, স্ট্র্যাটেজিক ওয়ারফেয়ার, কূটনীতি, ধর্মবিশ্বাস ও প্রতিশোধ... সব মিশে গেছে এই কাহিনীতে। এখানে বলে রাখা ভাল, বইয়ের শেষের দিকে সামুদ্রিক ঝড় এবং নৌযুদ্ধের একটা সিকোয়েন্স আছে, এমন রুদ্ধশ্বাস এবং ডিটেইলড বর্ননা আমি কোনদিন পড়িনি মনে হয়। রান্নাবান্না হোক অথবা ভাষা, নৌবিদ্যা হোক অথবা আলাপচারিতার ভাষা - কোথাও কোন খুঁত নজরে পড়ল না।
শেষে বলি, চারিত্রিক বিশ্লেষণ না করলেও বোঝা যায়, এই গল্পে প্রতিটা চরিত্রের একটা যাত্রা আছে। এই যাত্রা একান্তভাবে ব্যক্তিগত, কিন্তু কাহিনীর মূলস্রোতের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে ঠিকই। জীবন প্রতিটা চরিত্রকে বদলেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, ফলে তারা প্রায় রক্তমাংসের চরিত্রের মতোই জীবন্ত বলে মনে হয়েছে। সাদা হাতি পেগু অথবা পেত্নী করপূর্মঞ্জরী ও ব্যতিক্রম নয়। এই ক্যারেকটার আর্ক এই উপন্যাসকে অন্য স্তরে নিয়ে গেছে।
প্রায় তিনশ পাতার এই উপন্যাস আদতে আবহমান ইতিহাসের একটা জানলা ( ওয়ার্মহোল বলাটা কি বাড়াবাড়ি?) যেখান থেকে খুব সহজেই চলে যাওয়া যায় চারশ বছর আগের একটা সময়ে। সচক্ষে দেখে আসা যায় সন্দ্বীপ, সেগ্রাম, রোসাঙ্গা অথবা চাটিগাঁকে। মগ মোগল পর্তুগিজ ব্রিটিশ ওলন্দাজ বাঙালিদের জীবন অনুভব করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।
পাঠকদের কাছে কাম্য, বইটাকে সময় দেবেন। এই বই আপনার মনোযোগ দাবি করে। আমার বিশ্বাস, পাইয়া ফিরিঙ্গ ডর আপনাদের হতাশ করবে না।
পাইয়া ফিরিঙ্গ ডর
রাজর্ষি দাস ভৌমিক
সৃষ্টিসুখ
Published on August 01, 2020 11:51
আন্দালুসিয়ার শহরে একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে কয়েকটা বই নজরে...

আন্দালুসিয়ার শহরে একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে কয়েকটা বই নজরে পড়েছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজদের ভারতবর্ষে আসা নিয়ে লেখা, বিশেষত বাংলা ও বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের নানা দেশ আর রাজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করার কাহিনী। মুর রাজাদের জাহাজ ব্যবহার করে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীরা ভারতে পাড়ি দিয়েছিল, এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী সময়ে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল জলদস্যু হিসেবে। স্বাভাবিকভাবেই বইগুলো ছিল স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষায় লেখা।
যাই হোক, বাংলার এই ইতিহাস নিয়ে স্পেনের দোকানে সারি সারি বই দেখে আমি বেশ অবাকই হয়েছিলাম। সেই যুগের ইতিহাস ও পর্তুগিজ শাসকদের বাংলা ঔপনিবেশবাদ গড়ে তোলা নিয়ে বাংলায় খুব কম লেখাই চোখে পড়েছে। সমসাময়িক কালে এই প্রথম একটা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এসে সেই জায়গাটা ভরাট করল।
‘পাইয়া ফিরিঙ্গ ডর’ এক নিশ্বাসে পড়ে ওঠার জন্যে লেখা হয়নি। মগ, পর্তুগিজ, আরাকান, মোগলরা যখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সেই সময়টাকে পুঙ্খানুুঙ্খভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন রাজর্ষি। বিভিন্ন চরিত্র ও বহুস্তরীয় দৃষ্টিকোণ ফুটে উঠেছে কাহিনীর আঁকেবাঁকে। নন লিনিয়ার ন্যারেটিভকে দক্ষ ভাবে ব্যবহার করেছেন লেখক, ফলে বিভিন্ন কাহিনীর মাঝে বুনে তোলা সূত্র জুড়ে গেছে একে অপরের সঙ্গে, সময়ের ফাটলগুলো ভরাট হয়ে গেছে সাবলীলভাবে।
লেখাটা পড়তে আমার বেশ সময় লেগেছে, তার প্রধান কারণ এর ব্যাপ্তি ও ডিটেইটিং। এই আখ্যানের ভাঁজে ভাঁজে সূক্ষ্ম কারুকাজ আছে, নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রতিটা পরিসর, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের সামাজিক জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি। বস্তুত এই বিন্দুগুলো এই লেখার স্ট্রং পয়েন্ট, আগ্রহ থাকলে এই জায়গাগুলো দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মন দিয়ে পড়লে বোঝা যায়, তথ্যের খুঁটিনাটি ও সত্যতা সম্পর্কে লেখক কতটা যত্নবান! রাজর্ষি কোথাও ভাষাকে অযথা জটিল করেননি, কিন্তু বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা আর পরিবেশ তৈরি করার ক্ষমতা নিয়ে কোন কথা হবে না।
'পাইয়া ফিরিঙ্গ ডর' কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেতেই পারে, আবার সামাজিক অথবা প্রেমের উপন্যাস বললেও ভুল হবে না। এই বহুকৌণিক কাহিনীতে যেমন টিবাও, ভিশকু আর কাবালহোর মতন পর্তুগিজ দস্যু আছে, সেরকমই আছে নগেনের মত ভাগ্যান্বেষী বাঙালি, ধনী পরিবারের ছেলে শ্যামল, আধা ফিরিঙ্গি ওফেলিয়া। এমনকি জলার পেত্নী কর্পূর্মঞ্জরীও আছে। (এরকম বাস্তবভিত্তিক লিটারারি উপন্যাসে পেত্নী দেখে সত্যিই ভড়কে গিয়েছিলাম, ব্যাপারটা মেটাফর কি না বোঝার চেষ্টা করছি, ইতিমধ্যে আবিষ্কার করলাম এই অলৌকিক আখ্যান সহজ ভাবে জুড়ে গেছে মূল কাহিনীর সঙ্গে, কোথাও খাপছাড়া মনে হয়নি। সুতরাং সেই চিন্তায় অব্যাহতি দিলাম )
যাই হোক, আমার মতে, পাইয়া ফিরিঙ্গ ডর আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক উপন্যাস। আরো ভাল করে বলতে গেলে ভূরাজনৈতিক উপন্যাস। সপ্তদশ শতাব্দীতে জিও পলিটিকাল ফিকশন লেখা হত না নিশ্চয়ই, সে অর্থে এই কাহিনী বিরল। ক্ষমতা লাভ ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পাশাপাশি রাজনৈতিক সম্পর্ক, যুদ্ধের পরিকল্পনা, স্ট্র্যাটেজিক ওয়ারফেয়ার, কূটনীতি, ধর্মবিশ্বাস ও প্রতিশোধ... সব মিশে গেছে এই কাহিনীতে। এখানে বলে রাখা ভাল, বইয়ের শেষের দিকে সামুদ্রিক ঝড় এবং নৌযুদ্ধের একটা সিকোয়েন্স আছে, এমন রুদ্ধশ্বাস এবং ডিটেইলড বর্ননা আমি কোনদিন পড়িনি মনে হয়। রান্নাবান্না হোক অথবা ভাষা, নৌবিদ্যা হোক অথবা আলাপচারিতার ভাষা - কোথাও কোন খুঁত নজরে পড়ল না।
শেষে বলি, চারিত্রিক বিশ্লেষণ না করলেও বোঝা যায়, এই গল্পে প্রতিটা চরিত্রের একটা যাত্রা আছে। এই যাত্রা একান্তভাবে ব্যক্তিগত, কিন্তু কাহিনীর মূলস্রোতের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে ঠিকই। জীবন প্রতিটা চরিত্রকে বদলেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, ফলে তারা প্রায় রক্তমাংসের চরিত্রের মতোই জীবন্ত বলে মনে হয়েছে। সাদা হাতি পেগু অথবা পেত্নী করপূর্মঞ্জরী ও ব্যতিক্রম নয়। এই ক্যারেকটার আর্ক এই উপন্যাসকে অন্য স্তরে নিয়ে গেছে।
প্রায় তিনশ পাতার এই উপন্যাস আদতে আবহমান ইতিহাসের একটা জানলা ( ওয়ার্মহোল বলাটা কি বাড়াবাড়ি?) যেখান থেকে খুব সহজেই চলে যাওয়া যায় চারশ বছর আগের একটা সময়ে। সচক্ষে দেখে আসা যায় সন্দ্বীপ, সেগ্রাম, রোসাঙ্গা অথবা চাটিগাঁকে। মগ মোগল পর্তুগিজ ব্রিটিশ ওলন্দাজ বাঙালিদের জীবন অনুভব করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।
পাঠকদের কাছে কাম্য, বইটাকে সময় দেবেন। এই বই আপনার মনোযোগ দাবি করে। আমার বিশ্বাস, পাইয়া ফিরিঙ্গ ডর আপনাদের হতাশ করবে না।
পাইয়া ফিরিঙ্গ ডর
রাজর্ষি দাস ভৌমিক
সৃষ্টিসুখ
Published on August 01, 2020 11:51
July 12, 2020
ম্যাজিক রিয়ালিজমের গল্প
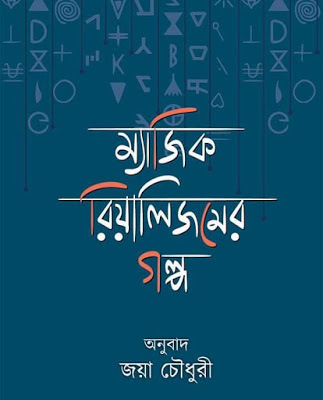
সৃষ্টিসুখ থেকে প্রকাশিত জয়া চৌধুরীর লেখা 'ম্যাজিক রিয়ালিজমের গল্প' অবশ্যই একটা আলোচনা দাবী করে। নিজে পড়ার সময় ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে হয়েছে, সেটাই সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। খুব সংক্ষেপে অবশ্য বলা যাবে না, কারণ আশি পাতার এই বইতে লেখিকা ল্যাটিন বুম যুগের তাবড় তাবড় সাহিত্যিকদের গল্পগুলো অনুবাদ করেছেন। মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, স্পেন, বলিভিয়া ইত্যাদি নানা দেশের লেখক লেখিকাদের কলমকে বুঝতে গেলে আশি পাতার একটি বই কিছুই নয় বিশেষ করে সূচীতে যখন খুয়ান রুলফো, ইসাবেলে আইয়েন্দে আর খুলিও কোরতাসারের মতন নাম মজুদ আছে। তাছাড়া নবীন যুগের দুই লেখকের কাহিনীও আছে এখানে। এদের অনেকেই পৃথিবী বিখ্যাত, বাস্তববাদ থেকে পরাবাস্তববাদ, সুরিয়ালিজম থেকে সাইন্স ফিকশন, সব ধারাতেই অবাধে বিচরণ করেন। এইবার আমি বইটার ভাল মন্দ ধাপে ধাপে বলার চেষ্টা করছি।
প্রথমত এরকম একটা অসাধারণ কাজের জন্যে প্রকাশক ও লেখিকাকে ধন্যবাদ। হিসপ্যানিক জগতের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ, খুব পরিচিত না হলে বইয়ের বাংলা অনুবাদও হয় না। ফলে সাধারণ পাঠক মার্কেস আর অন্য দু একজনের লেখা পড়েই থেমে যান। ল্যাটিন বুম যুগ অর্থাৎ ৬০ এবং ৭০ এর দশকে যে সাহিত্যিক বিপ্লব হয়েছিল স্প্যানিশ ভাষার সাহিত্যে, সেই নিয়ে আমরা খুব একটা বেশি জানি না। কার্লোস ফুয়েনতেস থেকে হোসে দনোসো, মার্কেস, মারিও লোসা সকলেই এই সময়ে পরিচিত হয়েছেন জগতের কাছে। ম্যাজিকল রিয়ালিজম নিয়ে এই সময়ে বেশিরভাগ সাহিত্যিক চর্চা করেছেন, সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে তুলে ধরেছেন গল্পের মাধ্যমে। সমস্যা হল যে যদি লেখক এবং লেখার সঙ্গে পরিচিতি না থাকে, তাহলে এই রেফারেন্সগুলো ধরা প্রায় অসম্ভব। ফলে গল্পে ম্যাজিক রিয়ালিজম কোথায়, বাক্যচয়ন আর প্রেক্ষাপটের অন্তরে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, সেটা বোঝা দুষ্কর। আমি কয়েকটা গল্পের উদাহরণ দিচ্ছি, তাহলে হয়ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।
যেমন আমপারো দাভিইয়ার লেখা গল্প El Huisped বা অতিথি। সাড়ে তিন পাতার এই গল্পে এক অতিথিকে নিয়ে হাজির করে বাড়ির কর্তা। তার স্ত্রী প্রথম থেকেই এই প্রাণীটিকে পছন্দ করছেন না, বরং ভয়ে ভয়ে আছেন। কিন্তু তার ভয়কে পাত্তা দেয়না বাড়ির কর্তা। প্রথম থেকে শেষ অব্দি বোঝা যায় না অতিথি কে? কুকুর না বেড়াল না প্যাঁচা? এক সময়ে বহু কষ্টে প্রাণীটির আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয় বাড়ির বাড়ির লোকজন।
ঘটনাটা বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেকেই ভাববে সেটা একেবারেই একটা ভয়ের কাহিনী, কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মেক্সিকান লেখিকা আমপারো দাভিইয়া আতঙ্ক, সাসপেন্স আর মৃত্যুর আবহাওয়া সৃজন করেন প্রতি গল্পে কিন্তু প্রতিটা চরিত্র আসলে রূপক অথবা মেটাফরিকাল। এই গল্পের আঙ্গিকে তিনি আঘাত করেন প্রাচীনপন্থী পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে, যেখানে নারীদের শুধুমাত্র শারীরিক নয়, মানসিক ভাবেও নির্যাতন করা হয়। অতিথি গল্পের প্যাঁচা অথবা কুকুর ( যাই হোক না কেন?) সে আসলে মেয়েটির স্বামীরই এক্সটেন্ডেড ভার্সন অথবা প্রতিরূপ। এমন ভাবেও ইন্টারপ্রেট করা যায় যে সমস্ত গল্পটা পুরুষ ও নারী সমাজের কনফ্লিক্ট নিয়ে, যেখানে জড়িয়ে আছে ভয়, দুঃখ, স্বাধীনতাবোধ ও রাগের নানা চিহ্ন। কিন্তু কিছুই যখন ঠিক করে লেখা নেই, তাহলে এই রহস্য সমাধান পাঠকের কাছে হবে কি করে? লেখিকা সেই সূত্রগুলো ছড়িয়ে রেখেছেন বিশেষ বিশেষ বাক্যের আড়ালে। এক একটা বাক্য আসলে ইঙ্গিত করে গল্পের ঊর্ধ্বে বলতে চাওয়া সত্যিটাকে। সেই কারণেই এখানে প্রতি লেখক অথবা লেখিকার নিজস্ব স্টাইল খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে অনুবাদ করা হয়ে ওঠে আরো কঠিন। যদি গল্পটা আত্মসাৎ করতে অথবা বাক্যের ভিতরে লুকিয়ে থাকা সূত্রের অবস্থান, গুরুত্ব আর প্রয়োজন না বোঝা যায়, অনুবাদ হলে নবীন পাঠক খুব সম্ভবত কিছুই বুঝতে পারবেন না।
হয়ত অনেকে ভাবছে এত ঝামেলার দরকার আছে কি? নিজের মত ইন্টারপ্রেট করে নিতে হবে যখন, সেটা যে যার নিজের মত করলেই চলে! উহুঁ! সেটা খুব কাজের হবে বলে মনে হয় না। কারণ ভঙ্গিমা ও বাক্যের আঙ্গিকে আড়াল করা দর্শনগুলো প্রত্যেকটি লেখকের একেবারে নিজস্ব। জীবন, সমাজ, মৃত্যু, রাষ্ট্র, ধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে প্রতিটা লেখকের নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে, তার অনেকটাই এসেছে তাদের নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। যেমন ইসাবেলে আইয়েন্দেকে চিলি থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিতে হয় ভেনেজুয়েলায়। জীবনের অনেকটা সময় তাকে প্রাণের ভয় নিয়ে কাটাতে হয়েছে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কারণে। আজকাল তিনি মার্কিন মুলুকে থাকেন। এই অভিজ্ঞতা তার লেখায় প্রতিফলিত হয়। 'বিকৃত মেয়েছেলে' গল্পটিতেও তার একটি ব্যাখা মেলে।ইসাবেলে বিশ্বাস করেন জীবনে কিছুই আগে থেকে বলা চলে না। কোন অভিজ্ঞতার তাত্ক্ষণিক প্রভাব যা হয়, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হয়ত সেটা বদলে দিতে পারে। একটি দুঃসহ অভিজ্ঞতা ভুলিয়ে কেউ হাসিখুশি জীবনযাপন করতে পারে, আবার ক্ষুদ্র কোন ঘটনা একজন মানুষকে সারজীবনের মত পাপবোধে দগ্ধ করতে পারে। একই ভাবে খুয়ান রুলফোর লেখা যে পড়েনি, তার জীবন সম্পর্কে না জানলে 'লগনচাঁদা' গল্পের অর্থ করা তার কাছে প্রায় অসম্ভব। মেক্সিকোয় থাকার সময়ে ক্রিস্টেরো রেবেলিয়নে তার বাড়ির লোকজনকে প্রচন্ড ভাবে ভুগতে হয়েছে। মেক্সিকান রেভলিউশন আর ক্যাথলিক পাদ্রীদের বাড়াবাড়ি নিয়মকানুনের ওপর তার রাগ ধরে গিয়েছিল প্রথম থেকেই। সেই নিয়েই স্যাটায়ার লিখেছেন ম্যাজিক রিয়ালিজমের মাধ্যমে। অপরাধবোধ আর জীবনের প্রতিটা সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ নিয়ে রহস্যচ্ছলে মজা আর কটুক্তি করে গেছেন।
প্রতিটা গল্প নিয়ে পৃথক ভাবে লেখা সম্ভব নয়। কথা হল বইটা কি তার উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে?
হ্যাঁ এবং না।
হ্যাঁ, কারণ এই লেখাগুলো তুলে আনা দরকার ছিল। প্রতিটা লেখাই অসম্ভব গভীর যদি সেই গভীরতার আন্দাজ পাওয়া যায়। সত্যি বলতে তিনটে লেখা আমার আগেই পড়া ছিল, বাকি প্রত্যেকটা আমায় ইংরেজিতে পড়তে হয়েছে বাংলাটা পড়ার পর। লেখিকা জটিল লেখাগুলিকে তুলে ধরতে ভয় পাননি মোটেই। বইয়ের শেষে তিনি একটা লেখক পরিচিতিও দিয়েছেন প্রতিটা লেখকের, ম্যাজিক রিয়ালিজম নিয়ে ভূমিকাতেও লিখেছেন বেশ খানিকটা। কিন্তু তাও অভাববোধ করলাম বেশ কয়েকটা বিষয়ে।
প্রথমত, অনুবাদ। কয়েকটা জায়গা ছাড়া কোন গল্প পড়েই মনে হয় না বাংলা গল্প পড়ছি। মনে হয় স্প্যানিশ গল্পের অনুবাদ পড়ছি আর সেটা পড়তে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছে। বাংলার পাঠকদের কথা ভেবে যদি লেখিকা বাংলা গল্পের মত করে লিখতেন তাহলে খুবই ভাল লাগত। আমরা আজকাল দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য আর ঋজু গাঙ্গুলীর অসাধারণ অনুবাদ পড়ে স্বভাব খারাপ করে ফেলেছি, অনুবাদের এই ঠোক্কর খাওয়া আমাদের খুবই অসহজ করবে। আমি কোন উদাহরণ দেব না, সেটা উচিৎও নয়। কিন্তু আমার মনে হয়েছে লেখিকা স্প্যানিশ ভাষা থেকে সরাসরি 'লিটারল ট্রানলেশন' করেছেন। সেটা ভাষার দিক থেকে একদম ঠিকঠাক হয়েছে ,কিন্তু বাংলা ভাষার পাঠকের জন্যে উপযুক্ত হয়নি। স্প্যানিশ ভাষার খানিকটা চর্চা করেছি বছর দুয়েক আগে, এটাও আমার মাথায় আছে যে এই গল্পগুলো অনুবাদ করা আসলে প্রচন্ড কঠিন। সাধারণ একটা গল্পের চেয়ে বেশিমাত্রায় জটিল তো বটেই, কিন্তু সেই চ্যালেন্জটা নিয়ে আরো সাবলীল ভাবে বাংলায় লেখাগুলো অনুবাদ করলে বইটা অন্য মাত্রা পেত। (আবার এও হতে পারে লেখিকা এরকম ভাবেই লেখাগুলো অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন, যাতে স্প্যানিশ ফ্লেভার রয়ে যায়। সেটা আমি বলতে পারব না।)
দ্বিতীয়ত, প্রতিটা লেখার একটা সংক্ষেপে এনালিসিস অবশ্যই দরকার ছিল। ম্যাজিক রিয়ালিজমের গল্প যখন, সেটা গল্পে কি করে এসেছে সেটা পাঠকের বোঝা জরুরী। আমাদের মত সাধারণ পাঠক যারা বিশ্বসাহিত্য নিয়ে খুব বেশী চর্চা করেনি, তাদের অন্তত সুবিধে হত। বাকি সব কিছুই ভাল। আশি পাতার বইটি যদি পাঠকদের এই লেখকদের অন্য লেখা পড়তে উত্সাহিত করে তাহলেই বইটার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।
প্রকাশক : সৃষ্টিসুখ
মূল্য : ১৩৫ টাকা
Published on July 12, 2020 10:47
সৃষ্টিসুখ থেকে প্রকাশিত জয়া চৌধুরীর লেখা 'ম্যাজিক রিয়ালিজ...
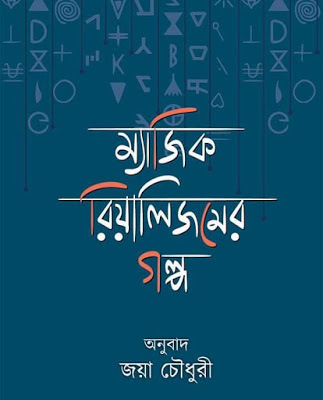
সৃষ্টিসুখ থেকে প্রকাশিত জয়া চৌধুরীর লেখা 'ম্যাজিক রিয়ালিজমের গল্প' অবশ্যই একটা আলোচনা দাবী করে। নিজে পড়ার সময় ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে হয়েছে, সেটাই সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। খুব সংক্ষেপে অবশ্য বলা যাবে না, কারণ আশি পাতার এই বইতে লেখিকা ল্যাটিন বুম যুগের তাবড় তাবড় সাহিত্যিকদের গল্পগুলো অনুবাদ করেছেন। মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, স্পেন, বলিভিয়া ইত্যাদি নানা দেশের লেখক লেখিকাদের কলমকে বুঝতে গেলে আশি পাতার একটি বই কিছুই নয় বিশেষ করে সূচীতে যখন খুয়ান রুলফো, ইসাবেলে আইয়েন্দে আর খুলিও কোরতাসারের মতন নাম মজুদ আছে। তাছাড়া নবীন যুগের দুই লেখকের কাহিনীও আছে এখানে। এদের অনেকেই পৃথিবী বিখ্যাত, বাস্তববাদ থেকে পরাবাস্তববাদ, সুরিয়ালিজম থেকে সাইন্স ফিকশন, সব ধারাতেই অবাধে বিচরণ করেন। এইবার আমি বইটার ভাল মন্দ ধাপে ধাপে বলার চেষ্টা করছি।
প্রথমত এরকম একটা অসাধারণ কাজের জন্যে প্রকাশক ও লেখিকাকে ধন্যবাদ। হিসপ্যানিক জগতের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ, খুব পরিচিত না হলে বইয়ের বাংলা অনুবাদও হয় না। ফলে সাধারণ পাঠক মার্কেস আর অন্য দু একজনের লেখা পড়েই থেমে যান। ল্যাটিন বুম যুগ অর্থাৎ ৬০ এবং ৭০ এর দশকে যে সাহিত্যিক বিপ্লব হয়েছিল স্প্যানিশ ভাষার সাহিত্যে, সেই নিয়ে আমরা খুব একটা বেশি জানি না। কার্লোস ফুয়েনতেস থেকে হোসে দনোসো, মার্কেস, মারিও লোসা সকলেই এই সময়ে পরিচিত হয়েছেন জগতের কাছে। ম্যাজিকল রিয়ালিজম নিয়ে এই সময়ে বেশিরভাগ সাহিত্যিক চর্চা করেছেন, সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে তুলে ধরেছেন গল্পের মাধ্যমে। সমস্যা হল যে যদি লেখক এবং লেখার সঙ্গে পরিচিতি না থাকে, তাহলে এই রেফারেন্সগুলো ধরা প্রায় অসম্ভব। ফলে গল্পে ম্যাজিক রিয়ালিজম কোথায়, বাক্যচয়ন আর প্রেক্ষাপটের অন্তরে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, সেটা বোঝা দুষ্কর। আমি কয়েকটা গল্পের উদাহরণ দিচ্ছি, তাহলে হয়ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।
যেমন আমপারো দাভিইয়ার লেখা গল্প El Huisped বা অতিথি। সাড়ে তিন পাতার এই গল্পে এক অতিথিকে নিয়ে হাজির করে বাড়ির কর্তা। তার স্ত্রী প্রথম থেকেই এই প্রাণীটিকে পছন্দ করছেন না, বরং ভয়ে ভয়ে আছেন। কিন্তু তার ভয়কে পাত্তা দেয়না বাড়ির কর্তা। প্রথম থেকে শেষ অব্দি বোঝা যায় না অতিথি কে? কুকুর না বেড়াল না প্যাঁচা? এক সময়ে বহু কষ্টে প্রাণীটির আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয় বাড়ির বাড়ির লোকজন।
ঘটনাটা বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেকেই ভাববে সেটা একেবারেই একটা ভয়ের কাহিনী, কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মেক্সিকান লেখিকা আমপারো দাভিইয়া আতঙ্ক, সাসপেন্স আর মৃত্যুর আবহাওয়া সৃজন করেন প্রতি গল্পে কিন্তু প্রতিটা চরিত্র আসলে রূপক অথবা মেটাফরিকাল। এই গল্পের আঙ্গিকে তিনি আঘাত করেন প্রাচীনপন্থী পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে, যেখানে নারীদের শুধুমাত্র শারীরিক নয়, মানসিক ভাবেও নির্যাতন করা হয়। অতিথি গল্পের প্যাঁচা অথবা কুকুর ( যাই হোক না কেন?) সে আসলে মেয়েটির স্বামীরই এক্সটেন্ডেড ভার্সন অথবা প্রতিরূপ। এমন ভাবেও ইন্টারপ্রেট করা যায় যে সমস্ত গল্পটা পুরুষ ও নারী সমাজের কনফ্লিক্ট নিয়ে, যেখানে জড়িয়ে আছে ভয়, দুঃখ, স্বাধীনতাবোধ ও রাগের নানা চিহ্ন। কিন্তু কিছুই যখন ঠিক করে লেখা নেই, তাহলে এই রহস্য সমাধান পাঠকের কাছে হবে কি করে? লেখিকা সেই সূত্রগুলো ছড়িয়ে রেখেছেন বিশেষ বিশেষ বাক্যের আড়ালে। এক একটা বাক্য আসলে ইঙ্গিত করে গল্পের ঊর্ধ্বে বলতে চাওয়া সত্যিটাকে। সেই কারণেই এখানে প্রতি লেখক অথবা লেখিকার নিজস্ব স্টাইল খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে অনুবাদ করা হয়ে ওঠে আরো কঠিন। যদি গল্পটা আত্মসাৎ করতে অথবা বাক্যের ভিতরে লুকিয়ে থাকা সূত্রের অবস্থান, গুরুত্ব আর প্রয়োজন না বোঝা যায়, অনুবাদ হলে নবীন পাঠক খুব সম্ভবত কিছুই বুঝতে পারবেন না।
হয়ত অনেকে ভাবছে এত ঝামেলার দরকার আছে কি? নিজের মত ইন্টারপ্রেট করে নিতে হবে যখন, সেটা যে যার নিজের মত করলেই চলে! উহুঁ! সেটা খুব কাজের হবে বলে মনে হয় না। কারণ ভঙ্গিমা ও বাক্যের আঙ্গিকে আড়াল করা দর্শনগুলো প্রত্যেকটি লেখকের একেবারে নিজস্ব। জীবন, সমাজ, মৃত্যু, রাষ্ট্র, ধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে প্রতিটা লেখকের নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে, তার অনেকটাই এসেছে তাদের নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। যেমন ইসাবেলে আইয়েন্দেকে চিলি থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিতে হয় ভেনেজুয়েলায়। জীবনের অনেকটা সময় তাকে প্রাণের ভয় নিয়ে কাটাতে হয়েছে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কারণে। আজকাল তিনি মার্কিন মুলুকে থাকেন। এই অভিজ্ঞতা তার লেখায় প্রতিফলিত হয়। 'বিকৃত মেয়েছেলে' গল্পটিতেও তার একটি ব্যাখা মেলে।ইসাবেলে বিশ্বাস করেন জীবনে কিছুই আগে থেকে বলা চলে না। কোন অভিজ্ঞতার তাত্ক্ষণিক প্রভাব যা হয়, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হয়ত সেটা বদলে দিতে পারে। একটি দুঃসহ অভিজ্ঞতা ভুলিয়ে কেউ হাসিখুশি জীবনযাপন করতে পারে, আবার ক্ষুদ্র কোন ঘটনা একজন মানুষকে সারজীবনের মত পাপবোধে দগ্ধ করতে পারে। একই ভাবে খুয়ান রুলফোর লেখা যে পড়েনি, তার জীবন সম্পর্কে না জানলে 'লগনচাঁদা' গল্পের অর্থ করা তার কাছে প্রায় অসম্ভব। মেক্সিকোয় থাকার সময়ে ক্রিস্টেরো রেবেলিয়নে তার বাড়ির লোকজনকে প্রচন্ড ভাবে ভুগতে হয়েছে। মেক্সিকান রেভলিউশন আর ক্যাথলিক পাদ্রীদের বাড়াবাড়ি নিয়মকানুনের ওপর তার রাগ ধরে গিয়েছিল প্রথম থেকেই। সেই নিয়েই স্যাটায়ার লিখেছেন ম্যাজিক রিয়ালিজমের মাধ্যমে। অপরাধবোধ আর জীবনের প্রতিটা সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ নিয়ে রহস্যচ্ছলে মজা আর কটুক্তি করে গেছেন।
প্রতিটা গল্প নিয়ে পৃথক ভাবে লেখা সম্ভব নয়। কথা হল বইটা কি তার উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে?
হ্যাঁ এবং না।
হ্যাঁ, কারণ এই লেখাগুলো তুলে আনা দরকার ছিল। প্রতিটা লেখাই অসম্ভব গভীর যদি সেই গভীরতার আন্দাজ পাওয়া যায়। সত্যি বলতে তিনটে লেখা আমার আগেই পড়া ছিল, বাকি প্রত্যেকটা আমায় ইংরেজিতে পড়তে হয়েছে বাংলাটা পড়ার পর। লেখিকা জটিল লেখাগুলিকে তুলে ধরতে ভয় পাননি মোটেই। বইয়ের শেষে তিনি একটা লেখক পরিচিতিও দিয়েছেন প্রতিটা লেখকের, ম্যাজিক রিয়ালিজম নিয়ে ভূমিকাতেও লিখেছেন বেশ খানিকটা। কিন্তু তাও অভাববোধ করলাম বেশ কয়েকটা বিষয়ে।
প্রথমত, অনুবাদ। কয়েকটা জায়গা ছাড়া কোন গল্প পড়েই মনে হয় না বাংলা গল্প পড়ছি। মনে হয় স্প্যানিশ গল্পের অনুবাদ পড়ছি আর সেটা পড়তে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছে। বাংলার পাঠকদের কথা ভেবে যদি লেখিকা বাংলা গল্পের মত করে লিখতেন তাহলে খুবই ভাল লাগত। আমরা আজকাল দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য আর ঋজু গাঙ্গুলীর অসাধারণ অনুবাদ পড়ে স্বভাব খারাপ করে ফেলেছি, অনুবাদের এই ঠোক্কর খাওয়া আমাদের খুবই অসহজ করবে। আমি কোন উদাহরণ দেব না, সেটা উচিৎও নয়। কিন্তু আমার মনে হয়েছে লেখিকা স্প্যানিশ ভাষা থেকে সরাসরি 'লিটারল ট্রানলেশন' করেছেন। সেটা ভাষার দিক থেকে একদম ঠিকঠাক হয়েছে ,কিন্তু বাংলা ভাষার পাঠকের জন্যে উপযুক্ত হয়নি। স্প্যানিশ ভাষার খানিকটা চর্চা করেছি বছর দুয়েক আগে, এটাও আমার মাথায় আছে যে এই গল্পগুলো অনুবাদ করা আসলে প্রচন্ড কঠিন। সাধারণ একটা গল্পের চেয়ে বেশিমাত্রায় জটিল তো বটেই, কিন্তু সেই চ্যালেন্জটা নিয়ে আরো সাবলীল ভাবে বাংলায় লেখাগুলো অনুবাদ করলে বইটা অন্য মাত্রা পেত। (আবার এও হতে পারে লেখিকা এরকম ভাবেই লেখাগুলো অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন, যাতে স্প্যানিশ ফ্লেভার রয়ে যায়। সেটা আমি বলতে পারব না।)
দ্বিতীয়ত, প্রতিটা লেখার একটা সংক্ষেপে এনালিসিস অবশ্যই দরকার ছিল। ম্যাজিক রিয়ালিজমের গল্প যখন, সেটা গল্পে কি করে এসেছে সেটা পাঠকের বোঝা জরুরী। আমাদের মত সাধারণ পাঠক যারা বিশ্বসাহিত্য নিয়ে খুব বেশী চর্চা করেনি, তাদের অন্তত সুবিধে হত। বাকি সব কিছুই ভাল। আশি পাতার বইটি যদি পাঠকদের এই লেখকদের অন্য লেখা পড়তে উত্সাহিত করে তাহলেই বইটার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।
প্রকাশক : সৃষ্টিসুখ
মূল্য : ১৩৫ টাকা
Published on July 12, 2020 10:47
আত্মহত্যার আত্মপক্ষ
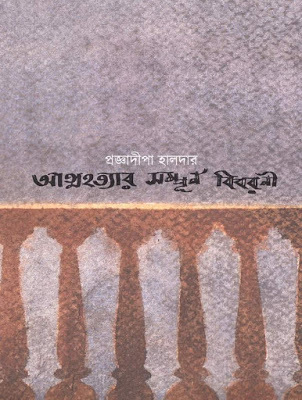
আমার প্রিয় বইয়ের অন্যতম হল পর্তুগিজ কবি ও লেখক ফের্নান্দো পেসোয়ার লেখা বই 'দ্য বুক অফ ডিসকোয়াইট'। তথ্যশূন্য এই আত্মজৈবনিক লেখাটা পেসোয়া প্রায় সারাজীবন ধরে লিখেছেন। প্রতিদিন রাতে এসে লিখতেন কয়েক পাতা। অস্পষ্ট রোজনামচা, খামখেয়াল অথবা দর্শন, চিন্তাভাবনা, আশাআকাঙ্খা, নিরাপত্তাহীনতা, বিষাদ... জড়মড় করে মিশে গেছে একে অপরের সঙ্গে। পেসোয়ার মৃত্যুর আশি বছরেরও পরে বইটা প্রকাশিত হয় এবং কয়েক বছরের অন্তরালে বিশ্বসাহিত্যে বরাবরের মত জায়গা করে নেয়।
'আত্মহত্যার সম্পূর্ণ বিবরণী' ইতিহাসে জায়গা করতে পারবে কি না আমার জানা নেই। হয়ত কয়েকজন আগ্রহী পাঠক বছর তিরিশ পর খুঁজে খুঁজে পড়বে বইটা, আবার হয়ত বছর দুয়েক পরেই আউট অফ প্রিন্টও হয়ে যেতে পারে। সব পাঠকের এই লেখা পছন্দ হবে কি না বলতে পারছি না, কিন্তু যদি কোন উত্সাহী পাঠক আকস্মিক ভাবে পাতাগুলো উল্টে যায়, বইটা তাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করবে বলে আমার বিশ্বাস।
প্রজ্ঞাদীপা হালদারের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। বছর তিনেক আগে তার ফেসবুক প্রোফাইলের সন্ধান পেয়েছিলাম কিভাবে যেন! কয়েকটা লেখা পড়ে অসম্ভব ভাল লেগেছিল। কাজেই অনেকের মত তার কিবোর্ডকেও ফলো করেছিলাম। আজ সোশ্যাল মিডিয়া ফেক নিউজ, প্রপোগান্ডা, ভার্চুয়াল যুদ্ধ, ট্রলিং আর বিপ্লবের জায়গা হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ স্ক্রল করলেই শরীর খারাপ করে। তাও পালাতে পারি না, তার একটা কারণ প্রজ্ঞাদীপার মত কিছু কলম। এর আগেও একটা বই লিখেছিলেন মনে হয়, সংগ্রহ করতে পারিনি। ভাগ্য ভাল, এই বইটা শেষমেস হাতে পেয়েছি।
আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু লেখিকার প্রতিভাকে 'ঈশ্বরপ্রদত্ত' ছাড়া আর কি বলব মাথায় আসছে না। একটাই কথা, সবাই পারে না। সম্ভব নয়।
মন আর আঙ্গুলের মাঝে দূরত্ব অনেকখানি। যেটা অনুভব করি, সেটা প্রকাশ করতে গেলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ভাষার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম! এই বইয়ের লেখাগুলো হৃদয় থেকে সরাসরি চুঁইয়ে পড়েছে বইয়ের পাতায়। কোন রকম ফিল্টারের তোয়াক্কা করেননি লেখিকা। কোনটা সাহিত্য আর কোনটা নয়, কোনটা ঠিক স্ট্রাকচার কোনটা নয়, পাঠক কি পড়বে কি নয় .. সেই সব চিন্তা তাঁর কোনদিনই ছিল বলে আমার মনে হয় না। ফলে বইটা নিখাদ সোনা (অথবা কাদার তাল, পাঠক যেভাবে নিতে চায়) হয়ে উঠেছে।
গত দুদিনে জ্বরের মধ্যে আমি পুরো বইটা একটানা পড়ে শেষ করলাম। হয়ত জ্বরের ঘোর ছিল বলেই, নাহলে এই বইয়ের গভীরতা আত্মসাৎ করা সম্ভব ছিল না। আবার এও বলা চলে বইটা আপাতসরল, কারণ ভাবনার সাবলীলতা কোন কিছুই জটিল হতে দেয় না। বইটা বিভক্ত করা হয়েছে ছয়টি ঋতুতে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। প্রতিটা ঋতুর সঙ্গে বদলে যাওয়া জীবন ও ভাবনার প্রকাশ। অতীতের নস্টালজিয়া আর স্মৃতিচারণ যেমন ঘুরে ঘুরে এসেছে, তেমনই এসেছে বিষাদ। আত্মহত্যার প্রয়োজনীয়তা। সিলভিয়া প্লাথ। জীবনানন্দ দাস। আর্নেস্ট হেমিঙওয়ে। অচ্যুত মণ্ডল। সমাজতত্ব নেই, দার্শনিকদের বিজ্ঞ প্রজ্ঞাপন নেই, মনোবিজ্ঞানের কককচি নেই, আছে বিলীয়মান জীবনের অবচুয়ারি। মানুষের জীবন, মফস্বলের জীবন। স্মৃতি আছে, মনখারাপ আছে, কবিতা আছে। আর আছে বিষাদ। স্বতফুর্ত সেই অনুপ্রবেশ।
পড়তে পড়তে আচমকা এক একটা জায়গা চলে আসে, যেখানে থেমে যেতে হয়। বার বার করে পড়ি।
যেমন বর্ষার এই জায়গাটা...
"ভেবে দেখ এমন প্রকল্প কত সহজ ছিল যেখানে তোমায় ভালোবাসা জানাতে রোজ লিখে ফেলব দু'হাজার শব্দ। মায়ের সঙ্গে আহ্লাদ, মাত্র আড়াইশো। বাবার স্নেহছায়ার জন্যে কৃতজ্ঞতায় শ পাঁচেক। এবং ঘৃণা জানাতে পাতার পর পাতা সাদা রাখাই অভিপ্রেত বোধ হয়। তাই পার্বতী বাউল গেয়ে ফ্যালেন উতর যাবি,সতর হবি, বলবি আমি যাই দখিনে। কিংবা হরিণা হরিণীর নিলয় না জানে। না জানা এই গৃহের সন্ধানে ঘুরেছি কত। বছর ঘুরে যায়, পছন্দের পায়রাখোপের সন্ধানে। আচ্ছা ধর যদি মাসগুলোকে এমন করে চেনা যায়, জুলাই- আগস্ট চিঠির মাস, সারা সকাল জুড়ে উঠোন ভরে চিঠির বৃষ্টি ঝরে। সেপ্টেম্বর - অক্টোবর উপেক্ষার মাস। তোমার চুলে বিশীর্ণ পাতারা অনুরোধের মত লেগে থাকে, তুমি রেলিংয়ে আংটি বাজিয়ে গাও 'পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোলে'। নভেম্বর - ডিসেম্বর- জানুয়ারি লাজলজ্জাহীন স্মৃতিমন্থন। ফেব্রুয়ারির দিন যেই উইড়্যা গেছে শুয়াপঙখী, আর পইড়্যা আছে মায়া। মার্চ- এপ্রিল-এর ক্যালেন্ডার জুড়ে ঋতুস্রাবের মতো লাল সব দিন, ছুটি ছুটি ছুটি, ভালরাক্ষস,চল পাহাড় বেরিয়ে আসি। মে-জুন কেবল বিশ্বাসঘাতকতা আর গৃহত্যাগের মাস মনে রেখো। ভাল লাগে না, বুঝেছ?"
ন্যারটিভের অভাবনীয় উপস্থাপনা আর স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া পরিচিত দৃশ্যের অসাধারণ বর্ণনা বার বার পাঠককে নিজের জীবনে উঁকি দিতে বাধ্য করে। গালিব আর অরণি বসুর কবিতার পাশাপাশি শৈশবের নানা চরিত্র আর ঘটনা এসে আদর করে দিয়ে যায়। দুপুর রোদ্দুরে বাড়িতে চলে আসা বাসনওয়ালিরা, একটা ছাদের মধ্যেই থাকা একাধিক ছোট ছোট ছাদ আর সেখানে কঞ্চির মাথায় জ্বালানো তারাবাজি, আকাশপ্রদীপ, কাচের আলমারিতে লুকিয়ে রাখা দিদিভাইয়ের খেলনা, স্মৃতির সুতো জড়ানো রেকাবি আর থালা যাতে খাবার না দিলে আমাদের অনেকেরই মাথা গরম হয়ে যেত। আশ্চর্য কিছু মিল! কিছু শাশ্বত সংস্কৃতি আর বিশ্বাসের অভ্যেস যা সময় পেরিয়ে গেলে অবান্তর মনে হয়, কিন্তু অধুনালুপ্ত সেই দৃশ্যকল্পগুলো ফিরে পাওয়ার আশায় ব্যাকুল হয়ে থাকি আজও। স্বীকার করি না।
এক জায়গায় লেখা--
"নতুন বছরের প্রথমদিন আমার কাছে কোন দ্যোতনা নিয়ে আসে না। আজ পয়লা বৈশাখ। আমি বলি একলা বৈশাখ। বৈশাখ একদিন একলা, আর আমি রোজ। সুতরাং ভাল থাক, ভাল আছি এইসব আমার আদ্যন্ত ভন্ডামি লাগে। উত্সবকে আমি চিনেছি তার নিঃশব্দ ব্যথাময়তায়। কোনও কিছু আয়ত্তে না রাখতে পারার অসহায়তায়। তবু অনেক বছর পর ভীষণ ভাল লাগছিল বলে আমি আজ ডিমের কুসুম রঙের শাড়ি পরেছিলাম। ঘর গুছিয়ে তুলতে গিয়ে আমার আকাশ -পাতাল আঁধার করা ঘুম পেতে থাকে। বচ্ছরকার দিনে আমি বসি বিছানায় আদুরে বেড়ালের মত গড়াই। বাইরের আমগাছে জোড়া শালিখ ভুরু কুঁচকে ভাবতে থাকে আমি বিষাদে না আনন্দে।"
এই বইয়ের আরো একটি পাওয়া হল পাতায় পাতায় করা অসাধারণ অলঙ্করণ। বাবলি পালের এই আঁকাগুলো লেখাগুলোকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। ছাদের তারে মেলা চাদর আর টব থেকে ঝুলে থাকা মানিপ্ল্যান্ট-এর ছবি অজান্তেই আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায় মফস্বলের পুরোনো বাড়ি অথবা ঝড়ের বিকেলে।
কিছু কিছু লেখার পাঠ প্রতিক্রিয়া হয় না। হওয়া সম্ভবও নয়। তাও যদি এটা পড়ে কেউ ঝুঁকি নিয়ে বইটা পড়তে চান, তাই লিখলাম।
আত্মহত্যার সম্পূর্ণ বিবরণী
প্রজ্ঞাদীপা হালদার
লিরিকাল বুকস
Published on July 12, 2020 10:46
আমার প্রিয় বইয়ের অন্যতম হল পর্তুগিজ কবি ও লেখক ফের্নান্দো...
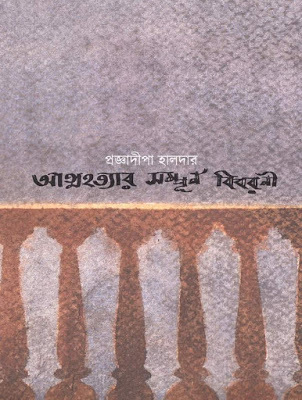
আমার প্রিয় বইয়ের অন্যতম হল পর্তুগিজ কবি ও লেখক ফের্নান্দো পেসোয়ার লেখা বই 'দ্য বুক অফ ডিসকোয়াইট'। তথ্যশূন্য এই আত্মজৈবনিক লেখাটা পেসোয়া প্রায় সারাজীবন ধরে লিখেছেন। প্রতিদিন রাতে এসে লিখতেন কয়েক পাতা। অস্পষ্ট রোজনামচা, খামখেয়াল অথবা দর্শন, চিন্তাভাবনা, আশাআকাঙ্খা, নিরাপত্তাহীনতা, বিষাদ... জড়মড় করে মিশে গেছে একে অপরের সঙ্গে। পেসোয়ার মৃত্যুর আশি বছরেরও পরে বইটা প্রকাশিত হয় এবং কয়েক বছরের অন্তরালে বিশ্বসাহিত্যে বরাবরের মত জায়গা করে নেয়।
'আত্মহত্যার সম্পূর্ণ বিবরণী' ইতিহাসে জায়গা করতে পারবে কি না আমার জানা নেই। হয়ত কয়েকজন আগ্রহী পাঠক বছর তিরিশ পর খুঁজে খুঁজে পড়বে বইটা, আবার হয়ত বছর দুয়েক পরেই আউট অফ প্রিন্টও হয়ে যেতে পারে। সব পাঠকের এই লেখা পছন্দ হবে কি না বলতে পারছি না, কিন্তু যদি কোন উত্সাহী পাঠক আকস্মিক ভাবে পাতাগুলো উল্টে যায়, বইটা তাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করবে বলে আমার বিশ্বাস।
প্রজ্ঞাদীপা হালদারের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। বছর তিনেক আগে তার ফেসবুক প্রোফাইলের সন্ধান পেয়েছিলাম কিভাবে যেন! কয়েকটা লেখা পড়ে অসম্ভব ভাল লেগেছিল। কাজেই অনেকের মত তার কিবোর্ডকেও ফলো করেছিলাম। আজ সোশ্যাল মিডিয়া ফেক নিউজ, প্রপোগান্ডা, ভার্চুয়াল যুদ্ধ, ট্রলিং আর বিপ্লবের জায়গা হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ স্ক্রল করলেই শরীর খারাপ করে। তাও পালাতে পারি না, তার একটা কারণ প্রজ্ঞাদীপার মত কিছু কলম। এর আগেও একটা বই লিখেছিলেন মনে হয়, সংগ্রহ করতে পারিনি। ভাগ্য ভাল, এই বইটা শেষমেস হাতে পেয়েছি।
আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু লেখিকার প্রতিভাকে 'ঈশ্বরপ্রদত্ত' ছাড়া আর কি বলব মাথায় আসছে না। একটাই কথা, সবাই পারে না। সম্ভব নয়।
মন আর আঙ্গুলের মাঝে দূরত্ব অনেকখানি। যেটা অনুভব করি, সেটা প্রকাশ করতে গেলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ভাষার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম! এই বইয়ের লেখাগুলো হৃদয় থেকে সরাসরি চুঁইয়ে পড়েছে বইয়ের পাতায়। কোন রকম ফিল্টারের তোয়াক্কা করেননি লেখিকা। কোনটা সাহিত্য আর কোনটা নয়, কোনটা ঠিক স্ট্রাকচার কোনটা নয়, পাঠক কি পড়বে কি নয় .. সেই সব চিন্তা তাঁর কোনদিনই ছিল বলে আমার মনে হয় না। ফলে বইটা নিখাদ সোনা (অথবা কাদার তাল, পাঠক যেভাবে নিতে চায়) হয়ে উঠেছে।
গত দুদিনে জ্বরের মধ্যে আমি পুরো বইটা একটানা পড়ে শেষ করলাম। হয়ত জ্বরের ঘোর ছিল বলেই, নাহলে এই বইয়ের গভীরতা আত্মসাৎ করা সম্ভব ছিল না। আবার এও বলা চলে বইটা আপাতসরল, কারণ ভাবনার সাবলীলতা কোন কিছুই জটিল হতে দেয় না। বইটা বিভক্ত করা হয়েছে ছয়টি ঋতুতে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। প্রতিটা ঋতুর সঙ্গে বদলে যাওয়া জীবন ও ভাবনার প্রকাশ। অতীতের নস্টালজিয়া আর স্মৃতিচারণ যেমন ঘুরে ঘুরে এসেছে, তেমনই এসেছে বিষাদ। আত্মহত্যার প্রয়োজনীয়তা। সিলভিয়া প্লাথ। জীবনানন্দ দাস। আর্নেস্ট হেমিঙওয়ে। অচ্যুত মণ্ডল। সমাজতত্ব নেই, দার্শনিকদের বিজ্ঞ প্রজ্ঞাপন নেই, মনোবিজ্ঞানের কককচি নেই, আছে বিলীয়মান জীবনের অবচুয়ারি। মানুষের জীবন, মফস্বলের জীবন। স্মৃতি আছে, মনখারাপ আছে, কবিতা আছে। আর আছে বিষাদ। স্বতফুর্ত সেই অনুপ্রবেশ।
পড়তে পড়তে আচমকা এক একটা জায়গা চলে আসে, যেখানে থেমে যেতে হয়। বার বার করে পড়ি।
যেমন বর্ষার এই জায়গাটা...
"ভেবে দেখ এমন প্রকল্প কত সহজ ছিল যেখানে তোমায় ভালোবাসা জানাতে রোজ লিখে ফেলব দু'হাজার শব্দ। মায়ের সঙ্গে আহ্লাদ, মাত্র আড়াইশো। বাবার স্নেহছায়ার জন্যে কৃতজ্ঞতায় শ পাঁচেক। এবং ঘৃণা জানাতে পাতার পর পাতা সাদা রাখাই অভিপ্রেত বোধ হয়। তাই পার্বতী বাউল গেয়ে ফ্যালেন উতর যাবি,সতর হবি, বলবি আমি যাই দখিনে। কিংবা হরিণা হরিণীর নিলয় না জানে। না জানা এই গৃহের সন্ধানে ঘুরেছি কত। বছর ঘুরে যায়, পছন্দের পায়রাখোপের সন্ধানে। আচ্ছা ধর যদি মাসগুলোকে এমন করে চেনা যায়, জুলাই- আগস্ট চিঠির মাস, সারা সকাল জুড়ে উঠোন ভরে চিঠির বৃষ্টি ঝরে। সেপ্টেম্বর - অক্টোবর উপেক্ষার মাস। তোমার চুলে বিশীর্ণ পাতারা অনুরোধের মত লেগে থাকে, তুমি রেলিংয়ে আংটি বাজিয়ে গাও 'পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোলে'। নভেম্বর - ডিসেম্বর- জানুয়ারি লাজলজ্জাহীন স্মৃতিমন্থন। ফেব্রুয়ারির দিন যেই উইড়্যা গেছে শুয়াপঙখী, আর পইড়্যা আছে মায়া। মার্চ- এপ্রিল-এর ক্যালেন্ডার জুড়ে ঋতুস্রাবের মতো লাল সব দিন, ছুটি ছুটি ছুটি, ভালরাক্ষস,চল পাহাড় বেরিয়ে আসি। মে-জুন কেবল বিশ্বাসঘাতকতা আর গৃহত্যাগের মাস মনে রেখো। ভাল লাগে না, বুঝেছ?"
ন্যারটিভের অভাবনীয় উপস্থাপনা আর স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া পরিচিত দৃশ্যের অসাধারণ বর্ণনা বার বার পাঠককে নিজের জীবনে উঁকি দিতে বাধ্য করে। গালিব আর অরণি বসুর কবিতার পাশাপাশি শৈশবের নানা চরিত্র আর ঘটনা এসে আদর করে দিয়ে যায়। দুপুর রোদ্দুরে বাড়িতে চলে আসা বাসনওয়ালিরা, একটা ছাদের মধ্যেই থাকা একাধিক ছোট ছোট ছাদ আর সেখানে কঞ্চির মাথায় জ্বালানো তারাবাজি, আকাশপ্রদীপ, কাচের আলমারিতে লুকিয়ে রাখা দিদিভাইয়ের খেলনা, স্মৃতির সুতো জড়ানো রেকাবি আর থালা যাতে খাবার না দিলে আমাদের অনেকেরই মাথা গরম হয়ে যেত। আশ্চর্য কিছু মিল! কিছু শাশ্বত সংস্কৃতি আর বিশ্বাসের অভ্যেস যা সময় পেরিয়ে গেলে অবান্তর মনে হয়, কিন্তু অধুনালুপ্ত সেই দৃশ্যকল্পগুলো ফিরে পাওয়ার আশায় ব্যাকুল হয়ে থাকি আজও। স্বীকার করি না।
এক জায়গায় লেখা--
"নতুন বছরের প্রথমদিন আমার কাছে কোন দ্যোতনা নিয়ে আসে না। আজ পয়লা বৈশাখ। আমি বলি একলা বৈশাখ। বৈশাখ একদিন একলা, আর আমি রোজ। সুতরাং ভাল থাক, ভাল আছি এইসব আমার আদ্যন্ত ভন্ডামি লাগে। উত্সবকে আমি চিনেছি তার নিঃশব্দ ব্যথাময়তায়। কোনও কিছু আয়ত্তে না রাখতে পারার অসহায়তায়। তবু অনেক বছর পর ভীষণ ভাল লাগছিল বলে আমি আজ ডিমের কুসুম রঙের শাড়ি পরেছিলাম। ঘর গুছিয়ে তুলতে গিয়ে আমার আকাশ -পাতাল আঁধার করা ঘুম পেতে থাকে। বচ্ছরকার দিনে আমি বসি বিছানায় আদুরে বেড়ালের মত গড়াই। বাইরের আমগাছে জোড়া শালিখ ভুরু কুঁচকে ভাবতে থাকে আমি বিষাদে না আনন্দে।"
এই বইয়ের আরো একটি পাওয়া হল পাতায় পাতায় করা অসাধারণ অলঙ্করণ। বাবলি পালের এই আঁকাগুলো লেখাগুলোকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। ছাদের তারে মেলা চাদর আর টব থেকে ঝুলে থাকা মানিপ্ল্যান্ট-এর ছবি অজান্তেই আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায় মফস্বলের পুরোনো বাড়ি অথবা ঝড়ের বিকেলে।
কিছু কিছু লেখার পাঠ প্রতিক্রিয়া হয় না। হওয়া সম্ভবও নয়। তাও যদি এটা পড়ে কেউ ঝুঁকি নিয়ে বইটা পড়তে চান, তাই লিখলাম।
আত্মহত্যার সম্পূর্ণ বিবরণী
প্রজ্ঞাদীপা হালদার
লিরিকাল বুকস
Published on July 12, 2020 10:46
ভূত নয়, ছায়া : অপচ্ছায়া
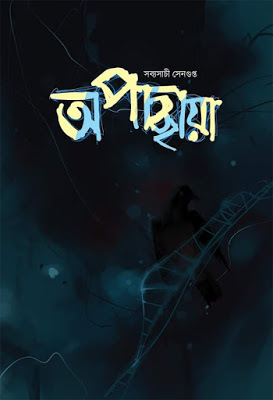
বইয়ের ভূমিকাতেই লেখক জানিয়েছেন, আনকোরা ও অশ্রুতপূর্ব বই কিনে পড়ার আগে তাঁর বাবা তাকে ভূমিকাটা পড়ে নিতে বলতেন। 'অপচ্ছায়া' বইটার ভূমিকা পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। সব্যসাচী সেনগুপ্তের লেখা অন্যান্য জনপ্রিয় বইগুলোও আগে পড়িনি। কিন্তু ভূতের বই বলেই কিনা কে জানে, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মোটেও ভুল করেনি।
গত কয়েক বছরের মধ্যে ভৌতিক ঘরানার যত বই পড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে, নিঃসন্দেহে বলতে পারি, 'অপচ্ছায়া' তাদের মধ্যে সেরা। কিন্তু একটা ডিসক্লেইমার আগে থেকেই দিয়ে রাখলাম, দাঁত কপাটি লাগা ভূতের গল্প পড়ার ইচ্ছে হলে এড়িয়ে যেতে পারেন। এই বইয়ের লেখায় ভয় দেখানো ভূতের দেখা প্রায় মিলবে না বললেই চলে। তন্ত্র নেই, বৌদ্ধ অপদেবতা নেই, রহস্যময় পুঁথি নেই, গ্রাফিক হরর নেই, নিদেনপক্ষে একটা আস্ত প্রেতাত্মাও ভাল করে দেখা দেয় না।
তাহলে আছে কি?
হুমম! সেটা বোঝানো মুশকিল। লেখক বইটা দুইভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে নিরেট ফিকশন গল্প, দ্বিতীয় ভাগে ইন্দ্রিয়তীত অভিজ্ঞতার বর্ণনা। অস্পষ্ট, আবছা অনুভূতির কাহিনী। কিন্তু যেই জিনিসটা এই বইয়ের সম্পদ, সেটা হল- হিন্দিতে যাকে বলে 'মাহৌল'। সেটিং অথবা মেজাজ বলাই যায়, কিন্তু মাহৌল কথাটা এই বইয়ের ক্ষেত্রে একবারে খাপে খাপ।
সমস্ত বই জুড়ে অনবদ্য এই মাহৌল তৈরী করেছেন লেখক। ন্যারেটিভের সাবলীল গতিময়তা আর দুর্দান্ত ডিটেইলিং একদম ঘাড় ধরে বসিয়ে রাখে পাঠককে। একবারের জন্যেও মন উচাটন হয় না। ভাষার বাঁধুনি এমনই পোক্ত, টক-ঝাল-মিষ্টি এতটাই পরিমাণ মতন যে ভূতের গল্পে ভূত না এলেও পাঠক উশখুশ করে না। ভূতের কথা ভুলে ততক্ষণে সে মজে গিয়েছে গল্পের পাতায়। হয়ত ডাক্তারি ছাত্রদের হোস্টেল, অথবা মফস্বলের রোজনামচা, কিংবা শৈশবের কোন স্মৃতি। আমাদের অবচেতনে থাকা খুঁটিনাটি কথা, যেগুলো বড্ড আপন হলেও কলমে ধরা যায় না, সেই অনুপ্রাসকে এত সহজে তুলে ধরতে আমি খুব বেশী লেখককে দেখিনি। এই মায়াজাল এমন বিস্তার হয়েছে সমস্ত বই জুড়ে, যে লেখাগুলো ভৌতিক না রম্যরচনা, স্মৃতিচারণ না কলাম, সেইসব ভাববার আগেই আপনি তরতর করে গল্পের শেষে পৌঁছে যাবেন আর ওভারের শেষ ইয়র্কর বলে ক্লিন বোল্ড হবেন। একটু গাটা যে শিরশির করবে না, সেটা বলতে পারছি না। (আমার বেশ ভয় ভয় লাগল বাবা।)
সব গল্পই যে দশে দশ তা অবশ্য নয়। 'আপাত ফিকশন' বিভাগের পাঁচটি গল্প অনুভূতির নানা তারে বাঁধা। কিন্তু কলমের দক্ষতায় রসস্বাদনে ছেদ পড়ে না। 'নিছক গল্প নয়' বিভাগের রচনাগুলো আরো তীক্ষ্ণ, তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। (তার একটা কারণ, প্রতিটা গল্পই একাধারে ব্যক্তিগত এবং কোন না কোন ভাবে লেখকের স্মৃতির অনেকটা দখল করে রয়েছে।)
বইটার আরো একটি বিশেষত্ব হল লেখকের রেঞ্জ। বইয়ের প্রথম গল্প খাঁটি সাধু ভাষায় লেখা, কিন্তু বইয়ের শেষ লেখায় যেতে যেতে সমস্ত আর্কটা ধরা পড়বে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলাম।
১ --
"দুর্ভাবনায় ভ্রূকুঞ্চন ক্রমশ গভীরতর হইতেছিল শিবশঙ্করের। তাবিজ কবচ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ চলিতেছিল মহামায়াপুরের জমিদারবাড়িতে। পালকি ছড়িয়া কাশীদেশের জ্যোতিষার্ণব, পদব্রজে, কামাখ্যাপীঠের তন্ত্রসিদ্ধ অথবা হিমালয়বাসী হঠযোগীর সশব্দ আগমন এক্ষণে এ স্থানের নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য। আজিকে এই রক্তাম্বর সন্যাসীর আগমন তাই এই আটচালাটিতে ঔৎসুক্যের পরিবর্তে বক্রোক্তিই অনিয়াছিল অধিক।"
২-
"মিনিট পাঁচেক বাদেই, ঠ্য়াকাস ঠ্য়াকাস শব্দে রুটির থালা, তড়কার প্লেট আর ন্যাতানো পেঁয়াজের বাটি নামিয়ে দিয়ে চলে যেত কর্মচারী। ঠকাঙ ঠোক্করে নামাত টাল খাওয়া এনামেলের খালি গেলাস। পড়পড়িয়ে জল ঢেলে দিয়ে যেত আকাশী রঙের জাগ থেকে। আর আমি পাঁচ আঙুলে রুটি ছিঁড়ে, তড়কায় মাখিয়ে, মুখে ঢুকিয়েই তড়িঘড়ি মচৎ কামড়াতাম পেঁয়াজ। ধাবার পেঁয়াজে কখনও কচাৎ শব্দ হয় না। এখানে পেঁয়াজ, হরবখত্ এট্টু এট্টু মিয়ানো।"
ক্লিশে রোমাঞ্চ আর শিহরণের ঊর্ধ্বে গিয়ে যদি অন্যরকম ভূতের গল্প পড়বেন খোঁজাখুঁজি করছেন, এই বইটা পড়ে দেখতে পারেন। মনে হয়, ঠকবেন না।
অপচ্ছায়া
লেখক - সব্যসাচী সেনগুপ্ত
প্রকাশক - সৃষ্টিসুখ
মূল্য - ১৭৫
Published on July 12, 2020 10:44
বইয়ের ভূমিকাতেই লেখক জানিয়েছেন, আনকোরা ও অশ্রুতপূর্ব বই ক...
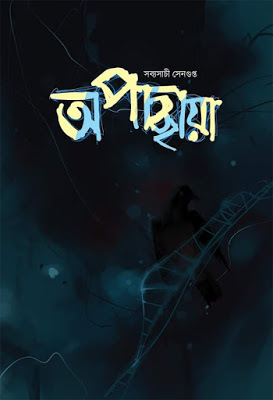
বইয়ের ভূমিকাতেই লেখক জানিয়েছেন, আনকোরা ও অশ্রুতপূর্ব বই কিনে পড়ার আগে তাঁর বাবা তাকে ভূমিকাটা পড়ে নিতে বলতেন। 'অপচ্ছায়া' বইটার ভূমিকা পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। সব্যসাচী সেনগুপ্তের লেখা অন্যান্য জনপ্রিয় বইগুলোও আগে পড়িনি। কিন্তু ভূতের বই বলেই কিনা কে জানে, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মোটেও ভুল করেনি।
গত কয়েক বছরের মধ্যে ভৌতিক ঘরানার যত বই পড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে, নিঃসন্দেহে বলতে পারি, 'অপচ্ছায়া' তাদের মধ্যে সেরা। কিন্তু একটা ডিসক্লেইমার আগে থেকেই দিয়ে রাখলাম, দাঁত কপাটি লাগা ভূতের গল্প পড়ার ইচ্ছে হলে এড়িয়ে যেতে পারেন। এই বইয়ের লেখায় ভয় দেখানো ভূতের দেখা প্রায় মিলবে না বললেই চলে। তন্ত্র নেই, বৌদ্ধ অপদেবতা নেই, রহস্যময় পুঁথি নেই, গ্রাফিক হরর নেই, নিদেনপক্ষে একটা আস্ত প্রেতাত্মাও ভাল করে দেখা দেয় না।
তাহলে আছে কি?
হুমম! সেটা বোঝানো মুশকিল। লেখক বইটা দুইভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে নিরেট ফিকশন গল্প, দ্বিতীয় ভাগে ইন্দ্রিয়তীত অভিজ্ঞতার বর্ণনা। অস্পষ্ট, আবছা অনুভূতির কাহিনী। কিন্তু যেই জিনিসটা এই বইয়ের সম্পদ, সেটা হল- হিন্দিতে যাকে বলে 'মাহৌল'। সেটিং অথবা মেজাজ বলাই যায়, কিন্তু মাহৌল কথাটা এই বইয়ের ক্ষেত্রে একবারে খাপে খাপ।
সমস্ত বই জুড়ে অনবদ্য এই মাহৌল তৈরী করেছেন লেখক। ন্যারেটিভের সাবলীল গতিময়তা আর দুর্দান্ত ডিটেইলিং একদম ঘাড় ধরে বসিয়ে রাখে পাঠককে। একবারের জন্যেও মন উচাটন হয় না। ভাষার বাঁধুনি এমনই পোক্ত, টক-ঝাল-মিষ্টি এতটাই পরিমাণ মতন যে ভূতের গল্পে ভূত না এলেও পাঠক উশখুশ করে না। ভূতের কথা ভুলে ততক্ষণে সে মজে গিয়েছে গল্পের পাতায়। হয়ত ডাক্তারি ছাত্রদের হোস্টেল, অথবা মফস্বলের রোজনামচা, কিংবা শৈশবের কোন স্মৃতি। আমাদের অবচেতনে থাকা খুঁটিনাটি কথা, যেগুলো বড্ড আপন হলেও কলমে ধরা যায় না, সেই অনুপ্রাসকে এত সহজে তুলে ধরতে আমি খুব বেশী লেখককে দেখিনি। এই মায়াজাল এমন বিস্তার হয়েছে সমস্ত বই জুড়ে, যে লেখাগুলো ভৌতিক না রম্যরচনা, স্মৃতিচারণ না কলাম, সেইসব ভাববার আগেই আপনি তরতর করে গল্পের শেষে পৌঁছে যাবেন আর ওভারের শেষ ইয়র্কর বলে ক্লিন বোল্ড হবেন। একটু গাটা যে শিরশির করবে না, সেটা বলতে পারছি না। (আমার বেশ ভয় ভয় লাগল বাবা।)
সব গল্পই যে দশে দশ তা অবশ্য নয়। 'আপাত ফিকশন' বিভাগের পাঁচটি গল্প অনুভূতির নানা তারে বাঁধা। কিন্তু কলমের দক্ষতায় রসস্বাদনে ছেদ পড়ে না। 'নিছক গল্প নয়' বিভাগের রচনাগুলো আরো তীক্ষ্ণ, তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। (তার একটা কারণ, প্রতিটা গল্পই একাধারে ব্যক্তিগত এবং কোন না কোন ভাবে লেখকের স্মৃতির অনেকটা দখল করে রয়েছে।)
বইটার আরো একটি বিশেষত্ব হল লেখকের রেঞ্জ। বইয়ের প্রথম গল্প খাঁটি সাধু ভাষায় লেখা, কিন্তু বইয়ের শেষ লেখায় যেতে যেতে সমস্ত আর্কটা ধরা পড়বে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলাম।
১ --
"দুর্ভাবনায় ভ্রূকুঞ্চন ক্রমশ গভীরতর হইতেছিল শিবশঙ্করের। তাবিজ কবচ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ চলিতেছিল মহামায়াপুরের জমিদারবাড়িতে। পালকি ছড়িয়া কাশীদেশের জ্যোতিষার্ণব, পদব্রজে, কামাখ্যাপীঠের তন্ত্রসিদ্ধ অথবা হিমালয়বাসী হঠযোগীর সশব্দ আগমন এক্ষণে এ স্থানের নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য। আজিকে এই রক্তাম্বর সন্যাসীর আগমন তাই এই আটচালাটিতে ঔৎসুক্যের পরিবর্তে বক্রোক্তিই অনিয়াছিল অধিক।"
২-
"মিনিট পাঁচেক বাদেই, ঠ্য়াকাস ঠ্য়াকাস শব্দে রুটির থালা, তড়কার প্লেট আর ন্যাতানো পেঁয়াজের বাটি নামিয়ে দিয়ে চলে যেত কর্মচারী। ঠকাঙ ঠোক্করে নামাত টাল খাওয়া এনামেলের খালি গেলাস। পড়পড়িয়ে জল ঢেলে দিয়ে যেত আকাশী রঙের জাগ থেকে। আর আমি পাঁচ আঙুলে রুটি ছিঁড়ে, তড়কায় মাখিয়ে, মুখে ঢুকিয়েই তড়িঘড়ি মচৎ কামড়াতাম পেঁয়াজ। ধাবার পেঁয়াজে কখনও কচাৎ শব্দ হয় না। এখানে পেঁয়াজ, হরবখত্ এট্টু এট্টু মিয়ানো।"
ক্লিশে রোমাঞ্চ আর শিহরণের ঊর্ধ্বে গিয়ে যদি অন্যরকম ভূতের গল্প পড়বেন খোঁজাখুঁজি করছেন, এই বইটা পড়ে দেখতে পারেন। মনে হয়, ঠকবেন না।
অপচ্ছায়া
লেখক - সব্যসাচী সেনগুপ্ত
প্রকাশক - সৃষ্টিসুখ
মূল্য - ১৭৫
Published on July 12, 2020 10:44
চরাচর ভুলিয়ে দেওয়া বইয়ের সন্ধান
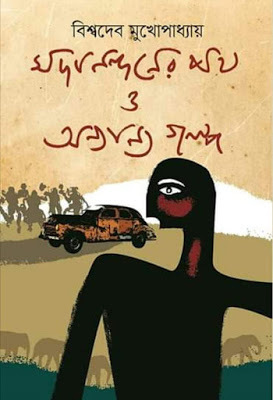
"এই বইটা আমার অসাধারণ লাগল।
প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?
মানে?
মানে, বইটা তো পছন্দ নাও হতে পারত।
কিন্তু বইটা ভাল বলেই তো আমার পছন্দ হয়েছে।
কিন্তু, পছন্দের তো রকমফের আছে। আমার যদি পছন্দটা অন্যরকম হত, তাহলে কি বইটা ভাল লাগত?
সেক্ষেত্রে বইটাও তো অন্যরকম হতে পারত।
কিন্তু বইটা তো এরকমই। আমার পছন্দও অন্যরকম নয়।
কিন্তু, আমি কি নিশ্চিত সেটাই সত্যি?"
এই কথোপকথনটি যদি আপনার ইন্টারেস্টিং মনে না হয়, ' সদানন্দনের পথ ও অন্যান্য ' বইটি আপনার কেমন লাগবে, সেটা আমি বলতে পারছি না। ব্যাক্তিগত ভাবে বলতে পারি, বইটা আমাকে প্রথমে বেদম আছাড় দিল, তারপর কুচি কুচি করে কাটল, শেষে গরম তেলে ভাজল। তেল থেকে আমাকে তোলার পর দেখলাম, আসলে কিছুই হয়নি।
' সদানন্দনের পথ ও অন্যান্য ' কয়েকটি ছোট গল্পের সঙ্কলন। গল্পগুলো আসলে কি ধারার সেটা নিয়ে আমার সংশয় আছে। কয়েক জায়গায় দেখলাম লেখাগুলোকে কল্পবিজ্ঞান তকমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শেষের গল্পটি বাদে কোন গল্পকেই আমি প্রচলিত কল্পবিজ্ঞানের আঙ্গিকে ভাবতে অক্ষম রইলাম।
তাহলে গল্পগুলো কি নিয়ে?
এককথায় বলতে গেলে গল্পগুলো হল, যাকে বলে - ইন্ট্রশপেক্সন অফ হিউম্যান রেস ইন স্পেসটাইম কন্টিনিউয়াম' অথবা অস্তিত্ববাদের ওপর ভিত্তি করে লেখা। একটা ক্ষুদ্র ঘটনা কীভাবে মানব জীবনের উর্ধ্বে গিয়ে জড়িয়ে থাকে সৃষ্টির নিয়মে, সেই প্রশ্ন, দ্বন্দ, শঙ্কা আর অনুসন্ধান নিয়েই বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকটি গল্প এঁকেছেন।
এঁকেছেন বলাই শ্রেয়, কারণ এধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে লিখলে কোনভাবেই পাঠকের অনুভূতিটা সাধারণত এরকম হয় না। আগে এধরনের বহু লেখা পড়তে গিয়ে লেখার জটিলতা, তত্ত্বের কচকচিতে নাজেহাল হয়েছি। আমারই দোষ, তাতে সন্দেহ নেই। আত্মদর্শন উপলব্ধি করতে গিয়ে যদি আমি বাংলা গল্পের ফ্লো নিয়ে বসে থাকি তাহলে কি জ্ঞান চক্ষু উন্মোচিত হয়? কিন্তু এই ম্যাচে রেফারি অন্য। খেলার নিয়মটাই আমূল পাল্টে দিয়েছেন বিশ্বদেববাবু। আর এটাই এই বইয়ের তুরুপের তাস।
প্রতিটা গল্প শুরু হয় সোজাসাপ্টা একটা প্লট দিয়ে। গ্রাম, শহর, মফঃস্বল, বন, জঙ্গল, পাহাড়। রক্তমাংসের চরিত্র। আটপৌরে সুঃখ-দুঃখ, দাম্পত্যের টানাপড়নে, অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস, হতাশা, পাগলামি নিয়ে চলতে থাকা যাপনের গল্প। আমাদের চেনাশোনা জগতের বাইরের কিছু উদ্ভট চরিত্র যে নেই তা নয়, কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড ও নিতান্ত স্বাভাবিক। এরকম চরিত্র বাংলা কিশোর উপন্যাসে আমরা আকছার দেখে থাকি। খানিকটা এগোতেই গল্পটা বেশ ইন্টারেস্টিং হয়ে পড়ে আর আপনি তুমুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন এবার কি হবে? বিলকুল রহস্য অথবা অলৌকিক গল্পের প্লট! সাবলীল ভাষায় দুর্দান্ত গতিতে গল্পটা এগোচ্ছে, হঠাৎ দু প্যারার মধ্যে প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে গল্প আপনাকে উল্টে ফেলে দিল। সামলে সুমলে উঠে বসেছেন, এমন সময় গল্পের রকেটের জানলা দিয়ে বাইরে দেখে আপনি পুরো ভ্যাবাচ্যকা খেয়ে গেলেন। কোথায় গ্রাম? মফস্বল? বন জঙ্গল? কোথায় পৃথিবী? ব্রহ্মাণ্ডের জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছেন পাঠক। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত্ সব একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন। রেগেমেগে চালককে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি হল? কোথায় আনলেন?' চালক হেসে বললেন, 'কোথায় আবার? যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন।' আপনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, বন জঙ্গল, পুকুর ডোবা, আমাদের বাড়ি, গেল কোথায়। এতো অনন্ত শূন্য!' জবাব এল 'অন্তত শূন্যই আমাদের বাড়ি, আবার বাড়িটাই অনন্ত শূন্য।'
এই হল এই বইয়ের ম্যাজিক। এর চেয়ে বেশী বোঝাবার কোন উপায় নেই, নিজে না পড়লে কেউ বুঝতে পারবেও না।
এরকম বইয়ের প্রতিক্রিয়া জানানোও চাপ, শুধু নিজের জন্যেই এটা লিখে রাখলাম। এমন একটা অসাধারণ কাজে ইচ্ছে করলেই ম্যাজিক রিয়ালিজম, সুরিয়ালিজম নানা তকমা দিয়ে দেওয়া যায়, আলোচনা চলতেই থাকে। অথচ বইটা খুবই কাজ চালানোর মত করে প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে হল। দেদার বানান ভুল। পেপারব্যাক এডিশনের তাৎপর্য ও আমি বুঝতে পারলাম না।
যারা এই লেখাটা পড়বেন, তাদের অনুরোধ করলাম, বইটা প্লিজ কিনে পড়ুন। সাধারণত এরকম বলি না। কিন্তু ব্যতিক্রম হলেই খুশী হই সবচেয়ে বেশি।
সদানন্দনের পথ ও অন্যান্য
বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়
ধ্যানবিন্দু
Published on July 12, 2020 10:42
"এই বইটা আমার অসাধারণ লাগল।প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?মানে?মানে, ব...
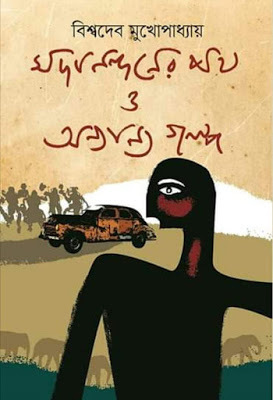
"এই বইটা আমার অসাধারণ লাগল।
প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?
মানে?
মানে, বইটা তো পছন্দ নাও হতে পারত।
কিন্তু বইটা ভাল বলেই তো আমার পছন্দ হয়েছে।
কিন্তু, পছন্দের তো রকমফের আছে। আমার যদি পছন্দটা অন্যরকম হত, তাহলে কি বইটা ভাল লাগত?
সেক্ষেত্রে বইটাও তো অন্যরকম হতে পারত।
কিন্তু বইটা তো এরকমই। আমার পছন্দও অন্যরকম নয়।
কিন্তু, আমি কি নিশ্চিত সেটাই সত্যি?"
এই কথোপকথনটি যদি আপনার ইন্টারেস্টিং মনে না হয়, ' সদানন্দনের পথ ও অন্যান্য ' বইটি আপনার কেমন লাগবে, সেটা আমি বলতে পারছি না। ব্যাক্তিগত ভাবে বলতে পারি, বইটা আমাকে প্রথমে বেদম আছাড় দিল, তারপর কুচি কুচি করে কাটল, শেষে গরম তেলে ভাজল। তেল থেকে আমাকে তোলার পর দেখলাম, আসলে কিছুই হয়নি।
' সদানন্দনের পথ ও অন্যান্য ' কয়েকটি ছোট গল্পের সঙ্কলন। গল্পগুলো আসলে কি ধারার সেটা নিয়ে আমার সংশয় আছে। কয়েক জায়গায় দেখলাম লেখাগুলোকে কল্পবিজ্ঞান তকমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শেষের গল্পটি বাদে কোন গল্পকেই আমি প্রচলিত কল্পবিজ্ঞানের আঙ্গিকে ভাবতে অক্ষম রইলাম।
তাহলে গল্পগুলো কি নিয়ে?
এককথায় বলতে গেলে গল্পগুলো হল, যাকে বলে - ইন্ট্রশপেক্সন অফ হিউম্যান রেস ইন স্পেসটাইম কন্টিনিউয়াম' অথবা অস্তিত্ববাদের ওপর ভিত্তি করে লেখা। একটা ক্ষুদ্র ঘটনা কীভাবে মানব জীবনের উর্ধ্বে গিয়ে জড়িয়ে থাকে সৃষ্টির নিয়মে, সেই প্রশ্ন, দ্বন্দ, শঙ্কা আর অনুসন্ধান নিয়েই বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকটি গল্প এঁকেছেন।
এঁকেছেন বলাই শ্রেয়, কারণ এধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে লিখলে কোনভাবেই পাঠকের অনুভূতিটা সাধারণত এরকম হয় না। আগে এধরনের বহু লেখা পড়তে গিয়ে লেখার জটিলতা, তত্ত্বের কচকচিতে নাজেহাল হয়েছি। আমারই দোষ, তাতে সন্দেহ নেই। আত্মদর্শন উপলব্ধি করতে গিয়ে যদি আমি বাংলা গল্পের ফ্লো নিয়ে বসে থাকি তাহলে কি জ্ঞান চক্ষু উন্মোচিত হয়? কিন্তু এই ম্যাচে রেফারি অন্য। খেলার নিয়মটাই আমূল পাল্টে দিয়েছেন বিশ্বদেববাবু। আর এটাই এই বইয়ের তুরুপের তাস।
প্রতিটা গল্প শুরু হয় সোজাসাপ্টা একটা প্লট দিয়ে। গ্রাম, শহর, মফঃস্বল, বন, জঙ্গল, পাহাড়। রক্তমাংসের চরিত্র। আটপৌরে সুঃখ-দুঃখ, দাম্পত্যের টানাপড়নে, অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস, হতাশা, পাগলামি নিয়ে চলতে থাকা যাপনের গল্প। আমাদের চেনাশোনা জগতের বাইরের কিছু উদ্ভট চরিত্র যে নেই তা নয়, কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড ও নিতান্ত স্বাভাবিক। এরকম চরিত্র বাংলা কিশোর উপন্যাসে আমরা আকছার দেখে থাকি। খানিকটা এগোতেই গল্পটা বেশ ইন্টারেস্টিং হয়ে পড়ে আর আপনি তুমুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন এবার কি হবে? বিলকুল রহস্য অথবা অলৌকিক গল্পের প্লট! সাবলীল ভাষায় দুর্দান্ত গতিতে গল্পটা এগোচ্ছে, হঠাৎ দু প্যারার মধ্যে প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে গল্প আপনাকে উল্টে ফেলে দিল। সামলে সুমলে উঠে বসেছেন, এমন সময় গল্পের রকেটের জানলা দিয়ে বাইরে দেখে আপনি পুরো ভ্যাবাচ্যকা খেয়ে গেলেন। কোথায় গ্রাম? মফস্বল? বন জঙ্গল? কোথায় পৃথিবী? ব্রহ্মাণ্ডের জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছেন পাঠক। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত্ সব একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন। রেগেমেগে চালককে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি হল? কোথায় আনলেন?' চালক হেসে বললেন, 'কোথায় আবার? যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন।' আপনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, বন জঙ্গল, পুকুর ডোবা, আমাদের বাড়ি, গেল কোথায়। এতো অনন্ত শূন্য!' জবাব এল 'অন্তত শূন্যই আমাদের বাড়ি, আবার বাড়িটাই অনন্ত শূন্য।'
এই হল এই বইয়ের ম্যাজিক। এর চেয়ে বেশী বোঝাবার কোন উপায় নেই, নিজে না পড়লে কেউ বুঝতে পারবেও না।
এরকম বইয়ের প্রতিক্রিয়া জানানোও চাপ, শুধু নিজের জন্যেই এটা লিখে রাখলাম। এমন একটা অসাধারণ কাজে ইচ্ছে করলেই ম্যাজিক রিয়ালিজম, সুরিয়ালিজম নানা তকমা দিয়ে দেওয়া যায়, আলোচনা চলতেই থাকে। অথচ বইটা খুবই কাজ চালানোর মত করে প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে হল। দেদার বানান ভুল। পেপারব্যাক এডিশনের তাৎপর্য ও আমি বুঝতে পারলাম না।
যারা এই লেখাটা পড়বেন, তাদের অনুরোধ করলাম, বইটা প্লিজ কিনে পড়ুন। সাধারণত এরকম বলি না। কিন্তু ব্যতিক্রম হলেই খুশী হই সবচেয়ে বেশি।
সদানন্দনের পথ ও অন্যান্য
বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়
ধ্যানবিন্দু
Published on July 12, 2020 10:42



