What do you think?
Rate this book
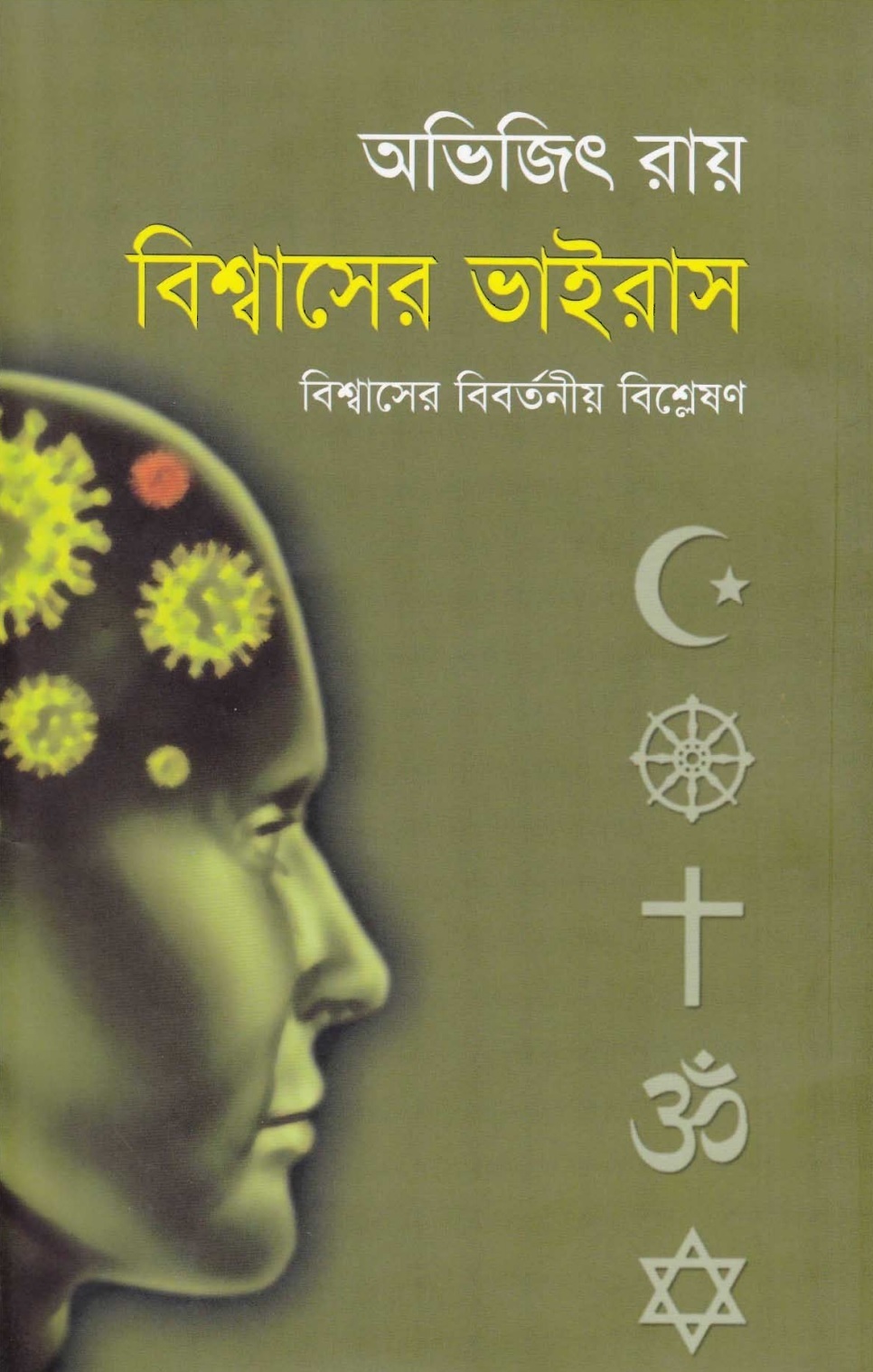
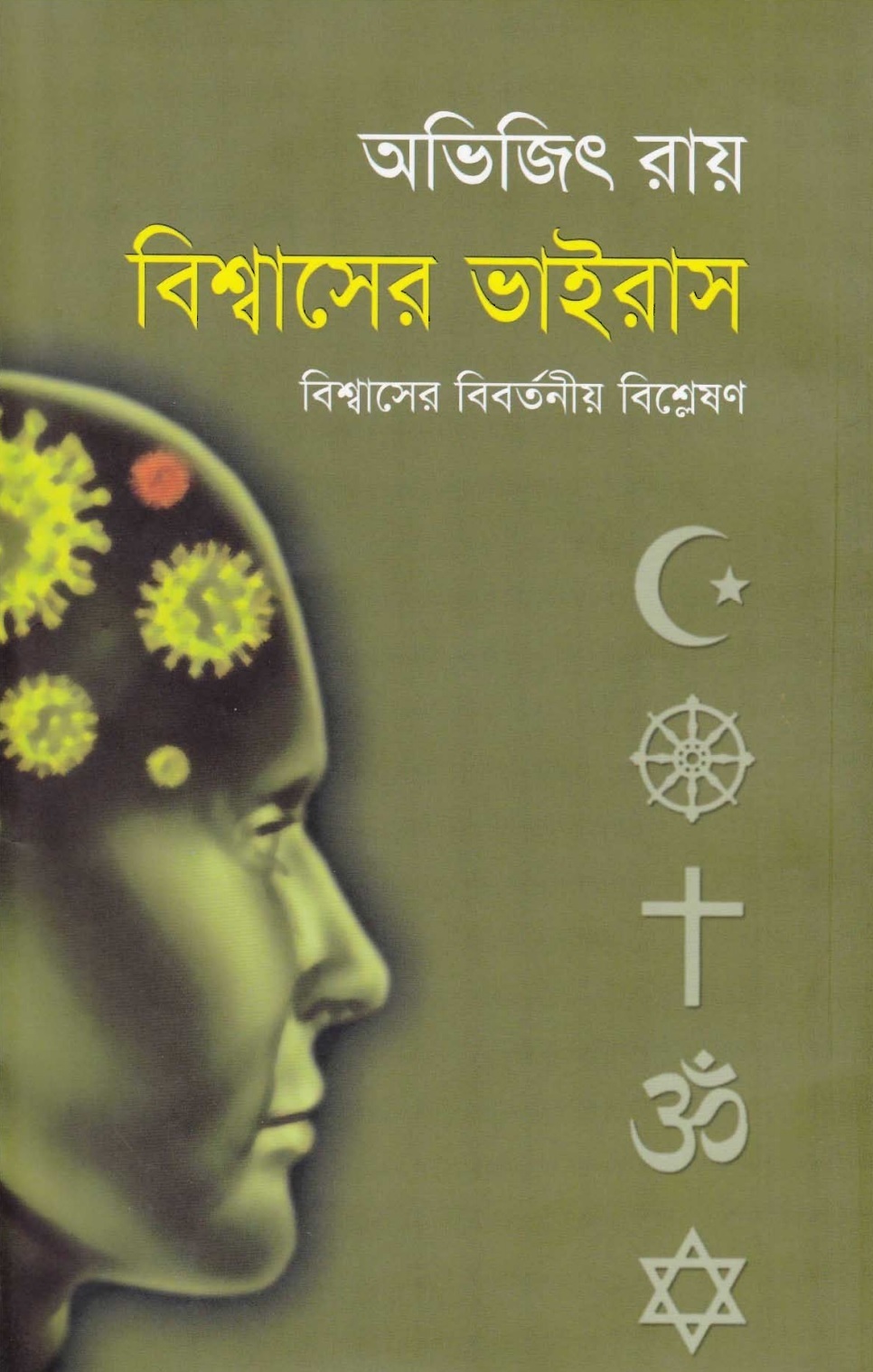
232 pages, Hardcover
First published February 1, 2014
‘আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে করো না। আমি শান্তি দিতে আসি নাই, এসেছি তলোয়ারের আইন প্রতিষ্ঠা করতে। আমি এসেছি মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে দাঁড় করাতে; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, বৌকে শাশুড়ির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি’ (মথি, ১০: ৩৪-৩৫)।
“… কিন্তু আমি বুঝি যে, ধর্মীয় প্রতিনিধিদের তরফ থেকে এমন ব্যবহার শুধু যে অপদার্থতা তা নয়, উপরন্তু মারাত্মক। কারণ মতবাদ যা নিজেকে পরিষ্কার আলোর মধ্যে বাঁচাতে না পেরে কেবলই অন্ধকারে গিয়ে লুকায়, তা নিশ্চিতভাবেই মানব প্রগতির গণনাতীত ক্ষতি করে।“
“একজন মানুষের নৈতিক আচার ব্যবহারের ভিত্তি হওয়া উচিৎ মানুষের প্রতি সহানুভূতি, শিক্ষা এবং সামাজিক বন্ধন বা সামাজিক দায়বদ্ধতা; কোন ধর্মীয় ভিত্তির প্রয়োজন নেই। মানুষকে সংযত করার জন্য যদি তাঁকে শাস্তির ��য় দেখাতে হয়, বা মৃত্যুর পরের পুরস্কারের লোভ দেখাতে হয়, তাহলে মানুষের কাছে তা হবে চরম লজ্জার ও অপমানের”।
১) বিবর্তন কাজ করে ব্যক্তির জিনের উপর, সমষ্টির উপরে নয়। ফলে সমষ্টির জন্য আপাত ক্ষতিকারক অনেক বৈশিষ্ট্যই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাতিল না হয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা দিতে গিয়ে টিকে থাকতে পারে।
২) প্যারাসাইটগুলো মস্তিষ্ক এবং দেহের জৈবিক প্রক্রিয়ার দখল নিয়ে নিতে পারে, যদিও তাদের উদ্ভব হয়তো একটা সময় ঘটেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রয়োজনে।
৩) জিন কিংবা মিমের বহির্সংক্রমণ ঘটতে পারে এবং যে কোন সময় আঞ্চলিক পরিবেশের ধংসসাধন ঘটতে পারে।
৪) জিন কিংবা মিমের ভাল কিংবা মন্দ বৈশিষ্ট্য পরিস্থিতিভেদে বিলুপ্ত হতে পারে কিংবা সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার মতো টিকে থাকতে পারে।
এবং সর্বোপরি –
৫) ধর্মীয় বিশ্বাস বিলুপ্ত না হয়ে টিকে থাকে, কারণ এগুলো আসলে ভাইরাস।
‘বইয়ের কথা মাথায় আসলেও সেটা যে এ বছরের মধ্যেই ঘটবে ঘুণাক্ষরেও মাথায় ছিল না। বইমেলা শুরুর দু’মাস আগে কেউ বইয়ের কাজ শুরু করে সেটা আবার শেষও করতে পারে নাকি? কিন্তু সেই অসম্ভব কাজই সম্ভব করে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন জাগৃতি প্রকাশনীর তরুণ প্রকাশক ফয়সল আরেফিন দীপন। তিনি যেভাবে তাগাদা দিয়ে আমার কাছ থেকে লেখা আদায় করে নিলেন, বই আকারে পাঠকদের সামনে তুলে ধরলেন, সেটাও ভাইরাসের চেয়ে কম আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। তিনি এতো কম সময়ের মধ্যে শুধু বইয়ের লেখা আদায়ই করেননি, মনোরম একটি প্রচ্ছদ করে মেলা শুরুর বহু আগেই ফেসবুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তার এহেন অবদান এবং নিরন্তর চাপাচাপি ছাড়া বইটি আলোর মুখ দেখতো না, তা হলফ করেই বলা যায়’।
“ভাইরাসমুক্ত জীবনের আস্বাদন কোন সুনির্দিষ্ট গন্তব্য নয়, বরং একটি চলমান যাত্রাপথের নাম। আমরা সবাই এই ভাইরাস দিয়ে কোন না কোন ভাবে আক্রান্ত এবং আমরা নিজেদের অজান্তেই বয়ে নিয়ে যাই অসুস্থ বিশ্বাস, মতামত কিংবা ধারণা। আমাদের অনেকের মাথাই আক্রান্ত করে ফেলা হয়েছে আমাদের শিশু বয়সেই আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পানপাত্র হাতে তুলে দিয়ে। আক্রান্ত মননকে প্রতিষেধক দিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ করে ফেলাই হবে আমাদের যাত্রাপথের লক্ষ্য। আমরা যদি বিশ্বাসের ভাইরাসের কুফলগুলো বুঝতে পারি, এ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকতে পারি, তবেই আমরা ভাইরাস মুক্ত সমাজ প্রত্যাশা করতে পারি’।